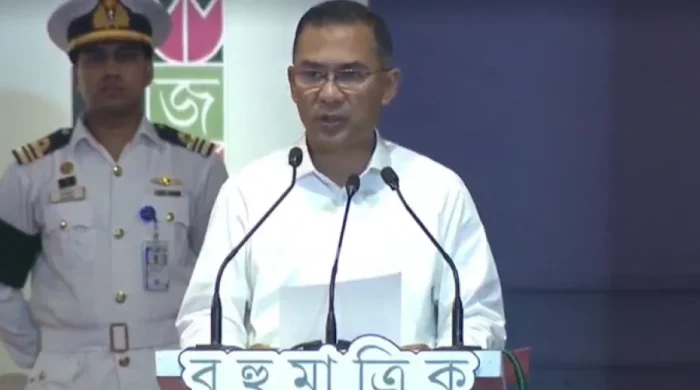সপ্তদশ শতকের সে মহামারী আজকের মহামারী তার প্রতিচ্ছবি
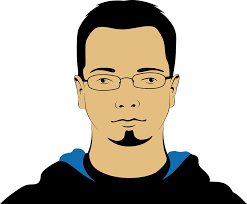
- আপডেট টাইম : রবিবার, ১৪ জুন, ২০২০
- ৩৫৪ বার

[১৬৬৪ সালে লন্ডনে দেখা দিয়েছিল ‘বিউবোনিক প্লেগ’ মহামারী যা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়েছিল। এই প্লেগ ইঁদুরের মাধ্যমে দ্রুত ছড়ায়। এর লক্ষণ হলো শীত লাগা, জ্বর এবং বগল ও তলপেট ফুলে যাওয়া। তখন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা স্যামুয়েল পেপিস যে ডায়েরি লিখেছিলেন, তার ভিত্তিতে এ লেখা। এর থেকে জানা যায়, সাড়ে ৩০০ বছর আগের সে মহামারী আর আজকের বিশ্বের করোনা জীবাণুঘটিত মহামারীর মধ্যে মিল অনেক। লেখক লোটজ-হেউমান যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা ইউনিভার্সিটির মধ্যযুগের শেষাংশ ও ‘রিফর্মেশন’-এর ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপক। গত ২৯ এপ্রিল ঈড়হংড়ৎঃরঁসহবংি.পড়স-এ প্রকাশিত কৌতূহলোদ্দীপক এ লেখার ভাষান্তর করেছেন মীযানুল করীম।]
এবার এপ্রিলের প্রথম দিকে লেখিকা জেন মিলার নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার পাঠকদের অনুরোধ জানান, তারা যেন ‘করোনাভাইরাস ডায়েরি’ লিখতে শুরু করেন। মিলার লিখেছিলেন, ‘কে জানে, হয়তো একদিন আপনার ডায়েরি বর্তমান সময়ের ব্যাপারে মূল্যবান তথ্য দেবে।’ সপ্তদশ শতকে ভিন্ন এক মহামারীর সময়ে ব্রিটেনের নৌবাহিনীর প্রশাসক স্যামুয়েল পেপিস সে কাজটি করেছিলেন। একঘেয়ে কাজ হলেও তিনি একাধারে ১৬৬০-১৬৬৯ সালের সময়কালে ডায়েরি রাখতেন। এ সময়ের মধ্যে লন্ডনে ভয়াবহ ‘বিউবোনিক প্লেগ’ সংক্রমিত হয়েছিল। মহামারীর ভীতি বরাবরই মানুষকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। তবে এত আগের কালের কারো জীবনে মহামারীর অভিজ্ঞতার এত বেশি বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই খুব কমই।
সে সময়ে কোনো ‘জুম’ মিটিং ছিল না, কিংবা ছিল না টেস্টিং বা ভেন্টিলেটর। সেটি সপ্তদশ শতাব্দীর লন্ডন। কিন্তু পেপিসের ডায়েরি থেকে প্রমাণিত হয়, মহামারীর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিস্ময়কর সামঞ্জস্য রয়েছে সেকাল ও একালে।
সঙ্কটের শিউরে ওঠা অনুভূতি
প্রথমে পেপিস এবং লন্ডনবাসীর জানার উপায় ছিল না যে, প্লেগের মতো মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সর্বপ্রথম, ১৬৬৪ সালের শেষে এবং ১৬৬৫ সালের শুরুর দিকে লন্ডন নগরীর বাইরের একটি দরিদ্র এলাকা সেন্ট গাইলসের গির্জায় প্লেগ দেখা দিয়েছিল।
সর্বপ্রথম, ১৬৬৫ সালের ৩০ এপ্রিল পেপিস উপলব্ধি করেন, ডায়েরিতে মহামারীর বিবরণ লিখে রাখা দরকার। তার ভাষায়, “এ নগরীতে প্লেগে আক্রান্ত হওয়ার বিরাট আতঙ্ক পরিলক্ষিত হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, দুই কি তিনটি বাড়ি ইতোমধ্যেই ‘শাটআপ’ হয়ে গেছে। বিধাতা আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।”
সে বছর জুনের প্রথম দিক পর্যন্ত পেপিস স্বাভাবিক জীবন কাটালেন। তখন তিনি প্রথমবারের মতো দেখলেন ঘরবাড়ি ‘শাটআপ’ করা হচ্ছে। এখনকার কোয়ারেন্টিনের প্রতিশব্দ সেটা। সে সময়ে ‘শাটআপ’ হওয়া বাড়ির দরজায় লাল ক্রসচিহ্ন এঁকে দেয়া হতো। সাথে লেখা থাকত, ‘বিধাতা আমাদের প্রতি দয়া করুন।’ নিজ চোখে এসব দেখে পেপিসের দুর্ভাবনা বাড়তে থাকে।
পেপিস শিগগিরই লক্ষ করেন, রাস্তা দিয়ে লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সৎকারের জন্য। চেনা-পরিচিত কয়েকজনও প্রাণ হারালেন যাদের মধ্যে তার নিজের ডাক্তারও ছিলেন।
আগস্টের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পেপিস নিজের ‘উইল’ তৈরি করে ফেললেন। লিখলেন তখন, ‘যদি এই উইলের সুবাদে স্রষ্টা এখন আমাকে এই পীড়িত সময় থেকে ডেকে নিয়ে যান, অনেক খুশি হবো।’ পরে সে মাসেই তিনি জনশূন্য রাজপথের কথা তুলে ধরে লিখেছেন, ‘এসব পথে এমন সব পথচারীর সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা দুনিয়া থেকে ছুটি নিয়েছেন।’
মৃতের সংখ্যার হিসাব
সে মহামারীর সময় লন্ডনে ‘দ্য কোম্পানি অব প্যারিশ ক্লার্কস’ প্রত্যেক সপ্তাহে কবর দেয়ার পরিসংখ্যান তুলে ধরে ‘নরষষং ড়ভ সড়ৎঃধষরঃু’ বের করত।
এ তালিকায় প্রকাশ করা হতো লন্ডনে কবর দেয়ার হিসাব। তবে আসলে কতজনের মৃত্যু ঘটেছে মহামারীতে তা জানা যেত না। নিঃসন্দেহে তালিকাটিতে মৃতের হিসাব দেখানো হতো কম করে। পেপিসের সময়ের সে তালিকা থেকেও বোঝা যায়, প্লেগের মহামারীতে মৃতের সংখ্যা বাড়ছিল ক্রমশ।
আগস্টের শেষ দিকে পেপিস ‘বিল অব মর্টালিটি’র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এতে উল্লেখ আছেÑ ৬ হাজার ১০২ জন প্লেগে প্রাণ হারিয়েছেন। তবে তার আশঙ্কা, প্রকৃত সংখ্যা হবে প্রায় ১০ হাজার। এর বড় কারণ, শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যারা মারা যেতেন, তাদের হিসাব রাখা হতো না। এক সপ্তাহ পরই, পেপিস দেখলেন, সরকারিভাবেই জানানো হচ্ছে, মহামারীতে এক সপ্তাহেই মারা গেছেন ৬ হাজার ৯৭৮ জন। এটা ছিল তার ভাষায়, ‘সর্বাধিক ভীতিপ্রদ সংখ্যা।’
সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, প্লেগ নিয়ন্ত্রণের সব ধরনের চেষ্টা-উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। কোয়ারেন্টিন কার্যকর করা হচ্ছিল না। লোকজন জড়ো হয়েছিল রয়্যাল এক্সচেঞ্জের মতো স্থানগুলোতে। সংক্ষেপে বলতে হয়, সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছিল না।
পেপিসের ভয় ছিল, প্লেগে মৃত ব্যক্তিদের শেষকৃত্যে যোগ দেয়া মানুষের ব্যাপারেও। তবে এ ধরনের কার্যক্রমে অংশ নেয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক নির্দেশ ছিল। প্লেগে মৃত্যুবরণকারী লোকদের কবর দেয়ার কথা রাতে। অথচ এ ব্যবস্থাও বজায় রইল না। পেপিস স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, ‘একেবারে দিনের আলোয় কবর দেয়া হচ্ছিল।’
নিরাময়ের জন্য মরিয়া
এখন কোভিড-১৯ রোগের চিকিৎসার জন্য কার্যকর ওষুধ নেই বললেই চলে। চিকিৎসা, তথা বিজ্ঞানের গবেষণা সময়সাপেক্ষ। অপর দিকে, করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত মানুষ এ জন্য যেকোনো পন্থা অবলম্বনে ইচ্ছুক। এ সুযোগে চিকিৎসার নামে প্রতারণা বর্তমানে ব্যাপক। এর মধ্যে আছে চা থেকে রূপা, এমনকি ফ্রান্সের ব্র্যান্ডি মদ আর গরুর মূত্রের ‘থেরাপি’।
পেপিস জীবিত ছিলেন, ‘বৈজ্ঞানিক বিপ্লব’কালে। তবে সেই ১৭তম শতাব্দীতে কারো জানা ছিল না প্লেগের কারণ হলো মাছির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ইয়ের্সিনিয়া পেস্টিস ব্যাকটেরিয়া। বরং সে আমলের বিজ্ঞানীদের অভিমত ছিল, “প্লেগ ছড়ায় সরধংসধ অর্থাৎ ‘মন্দ বাতাস’-এর মাধ্যমে। পচা জৈবপদার্থ এ ধরনের বাতাসের জন্মদাতা এবং দুর্গন্ধের সাহায্যে এটা চেনা যায়।” তখন প্লেগ মোকাবেলার যে কিছু পন্থা ছিল সর্বাধিক জনপ্রিয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- তামাকের ধোঁয়ার দ্বারা অথবা সংশ্লিষ্ট কারো নাকের সামনে কিছু ভেষজ উদ্ভিদ আর মসলা ধরে, বাতাসকে ‘বিশুদ্ধকরণ’।
তাই পেপিস সর্বপ্রথম তামাকের খোঁজ করলেন প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে। জুনের প্রথম দিকে, ‘শাটআপ’ হওয়া বাড়িঘর দেখে পেপিসের খারাপ ধারণা হলো নিজের এবং নিজের গায়ের গন্ধ সম্পর্কে। তখন তিনি বাধ্য হন তামাকের রোল কিনতে; এটা শোঁকা ও চিবানোর জন্য। জুলাই মাসে একজন অভিজাত পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তি তাকে দিলেন এক বোতল ‘প্লেগের পানি’। বিভিন্ন ধরনের গুল্ম মিশিয়ে ওষুধ হিসেবে এটা বানানো হতো। তবে এর কার্যকারিতা নিয়ে পেপিসের ছিল সন্দেহ। কফি হাউজে আলোচনা করা হয়েছিল লন্ডন শহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং এর নিরাময়ের উপায় সম্পর্কে। এতে অংশ নিয়ে পেপিস দেখতে পান, ‘কেউ বলছে এক কথা, কেউবা অন্য।’
মহামারীর সময়ে পেপিস নিজের মনের অবস্থা সম্পর্কে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি অবিরাম জানিয়েছেন, মন ভালো রাখার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। আজকের মতো কেবল ‘তার কিছু না হোক’- এ জন্য প্রয়াস চলছিল না। তখনকার চিকিৎসাবিজ্ঞানের থিওরি সম্পর্কে তিনি অবহিতও হচ্ছিলেন। এই তত্ত্ব¡মতে মানবদেহের চারটি কথিত ঐঁসড়ঁৎ ভারসাম্যহীন হয়ে গেলে রোগব্যাধি দেখা দেয়। এগুলো হচ্ছে- রক্ত, কৃষ্ণ পিত্ত, হরিদ্রা পিত্ত এবং শ্লেষ্মা।
ডাক্তাররা মনে করতেন, কালো রঙের পিত্তের মাত্রা অতিরিক্ত হলে মানুষ বিষণ্নতায় ভোগে। এতে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এ অবস্থায় স্যামুয়েল পেপিস নিজের নেতিবাচক আবেগগুলো চাপা দিতে চাইলেন। ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন, ‘বন্ধু-বান্ধব আর পরিচিতজনদের মধ্যে যারা প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাদের কথা শুনে বিষণ্নতার বিরাট শঙ্কা আমাকে গ্রাস করেছিল। তবে যতটা সম্ভব দুঃখের ভাবনা ঝেড়ে ফেলেছি।’
বিভ্রম ও ঝুঁকির ভারসাম্য
মানুষ সামাজিক প্রাণী এবং পরস্পর ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে বেঁচে থাকে। তাই এটা বিস্ময়কর নয় যে, করোনার এই মহামারীর সময়ে এত মানুষ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে। এ পরিস্থিতিতে, ঝুঁকি মোকাবেলার অব্যাহত প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যেমন, পরস্পর কতটা ঘনিষ্ঠ হলে ‘ঘনিষ্ঠতা’ বলা যায়? কিভাবে আমরা সংক্রমণ এড়াতে পারি এবং প্রিয়জনদের নিরাপদ রাখতে পারি কাণ্ডজ্ঞান না হারিয়ে? ঘরের কারো কাশি হলে আমাদের কী করা উচিত?
প্লেগ মহামারী আমলেও এমন ভীতিকর বিভ্রম ছিল ব্যাপক। পেপিস দেখলেন, তিনি লন্ডন ছেড়ে অন্যান্য শহরে ঢুকলে সেখানকার মানুষ দৃশ্যত নার্ভাস হয়ে পড়ছিলেন নবাগতদের সম্পর্কে। তার ভাষায় ‘ওরা আমাদের নিয়ে ভীত হয়ে পড়ে। এই ভয় এত বেশি যে, এতে আমাদের সমস্যা হলো।’ এটা মধ্য জুলাইয়ের কথা।
পেপিস নিজেও ছিলেন ভীতিজনিত বিভ্রমে আক্রান্ত। জুলাই মাসের শেষ দিকে তার চাকর উইলের মাথাব্যথা হয়েছিল হঠাৎ। পেপিস তা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন এটা ভেবে যে, চাকরটার প্লেগ হলে গোটা বাড়ি ‘শাটআপ’ করে দেয়া হবে। তাই তিনি অন্য সব চাকরকে দিয়ে অসুস্থ উইলকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, বাড়ির বাইরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল, তার প্লেগ হয়নি এবং পরদিনই তার প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল।
সেপ্টেম্বরের শুরুতে পেপিস একটি পরচুলা পরিধান করা থেকে বিরত রইলেন। লন্ডনের একটা এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ছিল ব্যাপক। সেখান থেকে তিনি পরচুলা বা উইগটা কিনেছিলেন। পেপিসের সন্দেহ ছিল, প্লেগে মারা যাওয়া লোকদের চুল দিয়ে সে পরচুলা বানানোর সম্ভাবনা বেশি। এটা কিভাবে মাথায় দিতে পারে লোকেরা?
তবুও পেপিস প্রয়োজনে ঝুঁকি নিয়েছিলেন। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে তিনি মহামারীর তোয়াক্কা না করে প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। সে বাড়ির চার পাশে, এমনকি প্রতিবেশীর ঘরেও ছিল প্লেগের বিস্তার। তবুও পেপিস এর ধার ধারেননি।
সারা বিশ্বেই মানুষ মহামারীতে মৃতের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। কারণ তখন মনে করা হয় যে, মহামারী বিদায় নিচ্ছে। পেপিসও তেমন আশা করেছিলেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মৃতের হার সর্বপ্রথম কমল। এক সপ্তাহ পরেই পেপিস দেখেন, ১৮০০রও বেশি কমে গেছে প্লেগে প্রাণহানির সংখ্যা।
পেপিসের মতো আসুন, আশাবাদী হই- শিগগিরই আমরা সুড়ঙ্গের আরেক প্রান্তে কিছু আলো দেখতে পাবো।