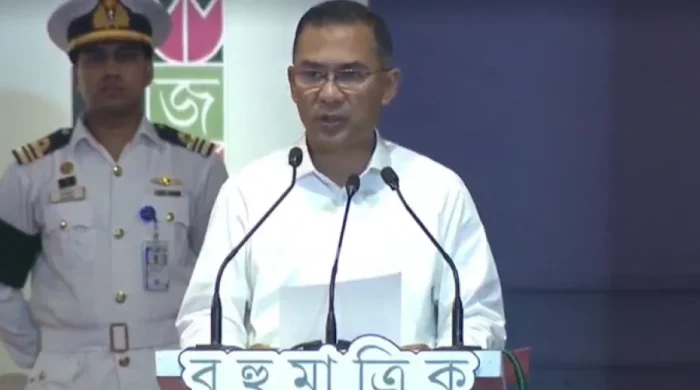জাতীয় রাজনীতি ও বাংলাদেশ
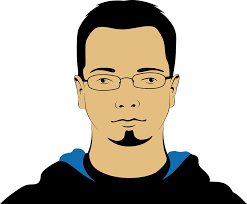
- আপডেট টাইম : শনিবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২০
- ২৮৫ বার

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক মতদর্শগত ২টি স্লোগান মূলত প্রাধান্য পায় : বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধের সমন্বয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনার উন্মেষ। এই দুই বিপরীতমুখী জাতীয় ও আদর্শিক বক্তব্য ও স্লোগান জাতিকে দ্বিধা-বিভক্ত করে, যা কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়। যেকোনো জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে স্বাধীনতা অর্জনের পর সেই স্বাধীন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রীয় সংবিধান তথা তার উন্নয়নের কর্মসূচির প্রতি যেসব নাগরিক আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং রাষ্ট্র উন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে সেই সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তথা রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বিতর্কিত বক্তব্য কিংবা মতপার্থক্য মোটেই কাম্য নয়। কারণ তা জাতীয় ঐক্য, সংহতি অগ্রগতি ও কল্যাণকে ব্যাহত করে। গণতন্ত্র পরমত সহিষ্ণুতা ও ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং নিজের মতাদর্শকে বলিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য যুক্তিসহকারে অন্যের কাছে পেশ করতে শিক্ষা দেয়। ভিন্ন মতাবলম্বীকে চারিত্রিক মাধুর্য, কর্মসূচিগত বাস্তবতা ও কর্মকৌশলগত নিপুণতা দিয়ে আপন করে নিতে হয়।
স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনয়নকারী দল ‘বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ’ দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সংগ্রাম ও ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েও ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সে ভূমিকা ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি। এটা নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাব ও ব্যর্থতা। ১৯৬৯ হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক দল হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন-শোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে এবং পরে বাংলাদেশীদের ক্ষমতার অংশগ্রহণের প্রশ্নেও শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ যে ভূমিকা পালন করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা দেশের মানুষ তাদের কাছে আরো অনেক কিছু আশা করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের পর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মন-মানসিকতায় এবং তদানীন্তন সরকার ও নীতিনির্ধারকগণ বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসাধারণের চিন্তাচেতনা ও বিশ্বাসের বিপরীতে তথায়-৮৫% মুসলিম আধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর হাজার বছরের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের তোয়াক্কা না করে, রাষ্ট্রীয় সংবিধানে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সংযোজন করেন, যার সাথে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সংগ্রামের কোনো কর্মসূচির মিল নেই।
এটি কিছুসংখ্যক ইসলাম ও মুসলিম শিক্ষা- সংস্কৃতিবিমুখদের সুকৌশলী ভূমিকারই প্রতিফলন যা আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের তথা শেখ মুজিবুর রহমানের গোটা জীবনের নির্ভীক, গণতান্ত্রিক ভূমিকা ও ধর্মীয় অনুভূতির, সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি যেমন ছিলেন গণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারবিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনার অধিকারী; তেমনি ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী ও মুসলিম জাতীয় সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও উদার দেশপ্রেমিক। তিনিই একমাত্র নেতা, যিনি স্বাধীনতার পর অনেক বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও তিনটি কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করে ইসলাম ও মুসলিম জাতীয় স্বার্থরক্ষা এবং দেশের সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণে আপসহীন মনোভাব প্রদর্শন করে স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ বিতর্কের অবসান করেছেন। স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ভারতীয় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) সম্মেলনে যোগদানের জন্য পাকিস্তানে গমন করেন এবং ওআইসি সদস্যপদ লাভ করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাপারে পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায় করে কূটনৈতিক বিজয় অর্জন করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী তথা মিত্রবাহিনীকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড হতে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যা পৃথিবীর অনেক নব্য স্বাধীন দেশের নেতা পারেননি। উদাহরণ- জাপান, ইংল্যান্ড, ভিয়েতনাম ইত্যাদি। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষ ভূমিকা নিয়েছে, তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার ঘোষণা।
মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান যখন এমনি জাতীয় ঐক্যের মনোভাবের পরিচয় দিলেন তখনই বিদ্বেষী ও শোষণনীতির অনুসারী কুচক্রীমহল শেখ মুজিব ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় সাংবিধানিকভাবে এবং কর্মকৌশলগতভাবে। একদিকে সাধারণ মুসলমানদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু প্রতীকী পরিবর্তন আনয়ন করে। ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী মহলটি সুকৌশলে শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমেই তা করাতে সক্ষম হয়। মহলটি এই সাংবিধানিক সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তার মতো সরলপ্রাণ লোকটিকে সারা জীবনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও দীর্ঘ গণতান্ত্রিক ভূমিকার বিপরীত কর্মসূচি অর্থাৎ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ ‘বাকশাল’ প্রতিষ্ঠা করে। এরই মাধ্যমে ওই সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীদের অর্থাৎ দলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই ব্যক্তিদের অভ্যন্তরীণ ভূমিকার কারণে দীর্ঘ ২৫ বছর কঠিন সংগ্রাম করে বাংলার গণমানুষের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্রের যে রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে আনেন, সেই সূর্যকে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংসদীয় গণতন্ত্রের পাদপিঠ জাতীয় সংসদে বসে অস্তমিত করা হলো। সে দিন পবিত্র সংসদে দাঁড়িয়ে বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব শেখ মুজিব ও তার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তির মুখে অকুতোভয় জেনারেল ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে পদত্যাগ করেছিলেন।
ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী ওই কুচক্রীমহল সরকারকে দেশের বাইরে ও ভেতরে দুর্বল করার কর্মসূচি নিতে বাধ্য করে। সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি, আনসার এবং বিডিআর থাকা সত্ত্বেও লালবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে ক্ষমতা প্রদান ও সেই পেশিশক্তি দিয়ে বিরোধী দলের বিপুল রাজনৈতিক নেতাকর্মীর ওপর গণহত্যা ও নির্যাতন পরিচালনা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সুদ, ঘুষ দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবকাঠামো ধ্বংস করা, এমনকি দেশের বৈদেশিক সাহায্য বন্ধের পাঁয়তারা করে জাতীয় দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি স্লান করার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হলো। এমনি অরাজক অবস্থার সুযোগে আওয়ামী লীগের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কিছুসংখ্যক নেতাকর্মীর সহযোগিতায় ইন্দো-মার্কিন চর ও শক্তির মদদে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারকে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ দিতে হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাথে আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতাকর্মীর সম্পৃক্ততা থাকা সত্ত্বেও শুধু মুজিব ও তার পরিবার কেন দায়ী? ১৫ আগস্ট রাতে অসংখ্য নেতার কিছু হয়নি; অথচ শুধু শেখ সাহেব এবং উনার পরিবারকেই শুধু নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হলো। ১৫ আগস্টের ঘটনার বেনিফিশিয়ারি হিসেবে খন্দকার মোশতাক ক্ষমতায় আরোহণ করেন, তার সাথে ক্ষমতার মসনদে গেলেন আব্দুল মালেক উকিল, মোহাম্মদ উল্লাহ, তাহের উদ্দিন ঠাকুর প্রমুখ। শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ নেতারা তারই রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে মন্ত্রীদের শপথ নিলেন।
একজন দরদি ও জনপ্রিয় দেশপ্রেমিক এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার নায়ককে সপরিবারে হত্যা করার পর দেশব্যাপী কোনো প্রতিবাদ কিংবা কোনো নিন্দা প্রস্তাবও নেয়া হলো না কেন? এই প্রশ্নের জবাব হিসেবে মনে হলো, হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের মূল দায়িত্ব ছিল তাদের, যারা রাজনৈতিক নেতাকর্মী এবং যারা স্লোগান দিতেন যে, ‘বঙ্গবন্ধু যেখানে, আমরা আছি সেখানে, মুজিব তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে’ এবং সেনাবাহিনীর তদানীন্তন প্রধানের রক্ষী বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন দলের যে নেতা তিনি ৩২নং রোড থেকে ৩০০-৫০০ গজ দূরে শেরেবাংলানগরে অবস্থান করেছিলেন। সেই দিন কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম) ছাড়া কোনো নেতাকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি। (সূত্র : বঙ্গভবনে পাঁচ বছর, মাহবুব আলম তালুকদার)।
আরো প্রশ্ন থেকে যায়, শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডে যদি রাজনৈতিক কারণে হয়েও থাকে, তবে বেগম মুজিব, রাসেল শিশুপুত্র ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়কে রেহাই দেয়া হয়নি। সেখানে অন্য নেতৃবৃন্দ কিভাবে নিরাপদে ঘাতকদের এত নিকটে থেকেও রেহাই পেলেন? আজকে যারা বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে বোন, আপা অথবা ভাতিজি ডেকে আপন করে নিজেদের স্বপ্নসাধ পূরণ করার চেষ্টা করছেন, তাদের অনেকেই পরোক্ষভাবে হলেও কি গভীর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত?
আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দলের এক জনসভায়, জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কাদের সিদ্দিকী বলেছিলেন, ‘আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকরীরা এখানে দলের মধ্যে অবস্থান করছেন এবং যতদিন আমার বোন শেখ হাসিনা ও তার প্রেসিডিয়াম নেতৃবৃন্দ চাইবেন না ততদিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার এ দেশের মাটিতে হবে না।’
তিনি আরো বলেন, এতে যদি আমার বোন আমাকে পুনরায় জেলে পাঠিয়ে দিতে বলেন, তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। একমাত্র আমি কাদের সিদ্দিকী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ও জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবো।’
সত্যিকার ষড়যন্ত্রকারীদেরকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা, শুধু তা-ই নয়, তাদেরকে সংসদের সদস্য বানানোসহ নেতৃত্বের চাবিকাঠি তাদের হাতে দেয়ার নীতিগত সমালোচনা করার প্রতিবাদে কাদের সিদ্দিকীকে বহিষ্কৃত আওয়ামী লীগার হিসেবে নতুন হুমকির সম্মুখে কোমরের গামছা মাথায় বেঁধে ২০০১ সালে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জিতে বিএনপিসহ চারদলীয় সরকারের সংসদ সদস্যদের সাথে শপথ নিতে হয়েছে। আরো উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে সেই সেনাবাহিনীর প্রধান নাটকীয়ভাবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সরকারগুলো তাকে বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের পদে দীর্ঘকাল সমাসীন রাখে।
প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের মতো স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যখনই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে হাত দিলেন এবং দেশের ভেতরে-বাইরে দেশের মান-সম্মান, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন নির্ভীক নেতা হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সেই আধিপত্যবাদের হোতারা পুনরায় অনুপ্রবেশ করে শেখ মুজিবের মতো জিয়ার বিরুদ্ধে তথা সমগ্র বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং কোন্দল সৃষ্টির মাধ্যমে সামরিক ও বেসামরিক পর্যায়ে ষড়যন্ত্র করে শেষ পর্যন্ত জিয়ার মতো নেতাকে নির্মমভাবে মুজিবের মতো হত্যা করে দ্বিতীয়বারের মতো সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।
অসংখ্য মুজিব প্রেমিক বাংলার মাটিতে ও আওয়ামী লীগে থাকা সত্ত্বেও ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবকে এবং তার পরিবারকে প্রাণ দিতে হয়েছে। একই কায়দায়, একই পদ্ধতিতে, একই মহলের প্ররোচনায় এবং ষড়যন্ত্রের কারণে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলে লুকিয়ে থাকা অনুচরদের ষড়যন্ত্রের মুখে বাংলার দ্বিতীয় অবিসংবাদিত নেতা এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এ দু’টি বিয়োগান্তক ঘটনা মূলত একই সূত্রে গাঁথা বলে ধরে নিতে হয়।
ষড়যন্ত্রকারী শক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সবসময় বজায় রাখার জন্য ও বাংলাদেশের উন্নয়ন তথা জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করার জন্য এই দুই জনপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক নেতাকে নিয়ে অহেতুক রাজনৈতিক অবস্থানগত বিতর্ক সৃষ্টি করে জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করছে এবং দেশের উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। মুজিব ১৮ কোটি মানুষের সম্পদ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্থপতি, তিনিই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা। জিয়াউর রহমান তেমনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষক এবং কোটি কোটি মানুষের সম্পদ। এই দু’জন দেশের জন্য জাতির জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সংগ্রাম করে গেলেন ও জীবন দিয়ে গেলেন তাদের কেউ কোনো দলের বা ব্যক্তির সম্পদ মনে করা রাজনৈতিক বোকামি। দু’জন নেতাই জীবন উৎসর্গ করে দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই এ দুই ব্যক্তির মর্যাদা নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক বিতর্কের অবসান হওয়া দরকার। একদল কারো ছবি তুলবেন আর অপরদল এসে বাধা দেবেন, একদল দেবেন ফুলের মালা আর একদল জুতার মালা, একদল পূজা করবেন আর একদল পোড়াবেন, একদল আনন্দমিছিল করে কেক খাবেন আরেকদল হরতাল দিয়ে জাতীয় জীবনে দুর্ভোগ আনবেন। এগুলোর আশু অবসান হওয়া উচিত। জাতীয় জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে আমরা স্বাধীনতার ৪৯ বছর পরও সমাধান করতে পারিনি, আধিপত্যবাদী মহলের ষড়যন্ত্রের কারণে।
একজন মুসলমানের দৃষ্টিতে কুরআনের বর্ণনানুযায়ী ‘মুসলিম জাতির পিতা’ হজরত ইবরাহিম (আ:)। এ বিষয়ে কারো কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু সেটি জানা সত্ত্বেও ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের জাতির জনক নিয়ে পাকিস্তান আমলে কোনো ধরনের বিতর্ক হয়নি, আজো বিতর্ক নেই। আর আমরা যারা মুজিব প্রেমিক হয়েও সময়মতো সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছি এবং তাদের অপকর্মের মাধ্যমেই তিনি বিতর্কিত হয়েছেন। মৃত মুজিবকে শুধু নিজেদের রাজনৈতিক হাতিয়ার ও ব্যক্তিগত বা দলীয় সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অপর পক্ষে জিয়াকেও কারো ব্যক্তিগত বা দলীয় সম্পদ করা ঠিক নয়। এই দুই মহান ব্যক্তিদ্বয়ের একটি জাতিগত ও সাংবিধানিক অবস্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে থাকা উচিত এবং বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত।
শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের এ জাতির প্রতিষ্ঠাতা অর্থাৎ, সাংবিধানিকভাবে সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করা যেতে পারে এবং জিয়াউর রহমানকে মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক হিসেবে সাংবিধানিক মর্যাদা দেয়া যেতে পারে এবং উভয়ের জন্ম ও মৃত্যুদিবসকে জাতীয়ভিত্তিক বিতর্কহীনভাবে পালন করে তাদের মূল্যবান ও কর্মময় জীবনের মূল্যায়ন করে জাতি অনুপ্রেরণা পেতে পারে।
লেখক : সহকারী অধ্যাপক, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, অব বাংলাদেশ