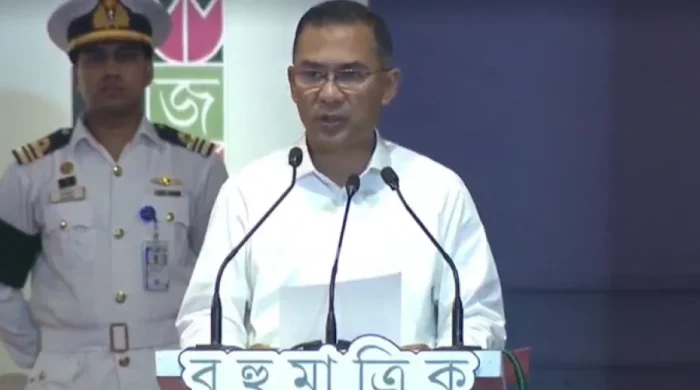অর্থ পাচারের সম্ভাব্য নতুন গন্তব্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে
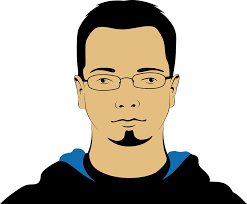
- আপডেট টাইম : রবিবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২১
- ২১৩ বার

বাংলাদেশ থেকে উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে অর্থ পাচারের ঘটনা নতুন নয়। পাশাপাশি এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সরকারের এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাও নতুন কিছু নয়। তারপরও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যখন এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তখন তা নিয়ে বিচ্ছন্নভাবে হলেও আলোচনা হয়। গত ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের অর্থ পাচার নিয়ে ওয়ায়শিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ছয় বছরে বাংলাদেশ থেকে ৪ লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। পাচারকৃত টাকার বার্ষিক গড় পরিমাণ হলো প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা। পাঁচ বছর আগের একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল, ২০০৬ থেকে ২০১৫ সাল এই ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ২৯ হাজার ৯৫৬ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে বছরপ্রতি পাচারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ হাজার কোটি টাকার উপরে। পরিসংখ্যান বলছে, অর্থ পাচারের প্রবণতা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে অর্থ পাচার নিয়ে প্রকাশিত রিপোর্টের ওপর ২১ ডিসেম্বর যুগান্তর একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। অর্থ পাচার রোধে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই অস্পষ্ট। অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশ জাতিসংঘে নিয়মিতভাবে বার্ষিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তথ্য দিয়ে আসছিল। কিন্তু ২০১৫ সালের পর থেকে তারা আর কোনো তথ্য সরবরাহ করছে না। ফলে জিএফআই ২০১৫ সালের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।
অর্থ পাচারের মূল মাধ্যমটি হলো আমদানি-রপ্তানি। আমাদের দেশের অর্থ পাচারের ৮০ শতাংশই ঘটে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে। প্রচলিত নিয়মে এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ যায়, বিনিময়ে আসে পণ্য বা সেবা। সেক্ষেত্রে কম দামি পণ্য বেশি দাম দেখিয়ে অর্থ পাচার করা হয়। বিদেশি রপ্তানিকারকরা বাংলাদেশের আমদানিকারকদের বিদেশি অ্যাকাউন্টে বাড়তি টাকা জমা করে। আবার রপ্তানির বেলায় বেশি দামের পণ্যের কম দাম দেখানো হয়। বিদেশের আমদানিকারকরা দেশীয় রপ্তানিকারকদের বিদেশি অ্যাকাউন্টে বাড়তি টাকা জমা করে দেয়। ২০১৫ সালে বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য হয়েছে, তার প্রায় ১৮ শতাংশ পাচার হয়ে গেছে, যার পরিমাণ ১ হাজার ১৮৭ কোটি ডলার বা দেশীয় মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা। এই বিপুল অঙ্কের টাকা তিনটি পদ্মা সেতুর মোট নির্মাণ ব্যয়ের চেয়েও বেশি।
অর্থ পাচারের ধারাবাহিক বৃদ্ধির পরিমাণটি সহজেই অনুমেয়। ২০১৩ সালে ছিল ৯৩৪ কোটি ডলার; এর আগের বছর ২০১২ সালে ৭৬৪ কোটি ডলার; ২০১০ সালে ছিল ৬৮৪ কোটি এবং ২০০৯ সালে ছিল ৫১২ কোটি ডলার। ১০ বছরে পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ বছরে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এটি নিশ্চয়ই একটি হতাশাব্যঞ্জক চিত্র।
অর্থ পাচারে দিক থেকে বাংলাদেশ এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। অর্থ পাচারের ফলে দেশে অভ্যন্তরীণভাবে বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। এক সময় বাংলাদেশের মোট বিনিয়োগের ৮০ শতাংশই ছিল বেসরকারি। কিন্তু বর্তমানে তা কমে ৭৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, বিনিয়োগকারীরা দেশে অর্থ বিনিয়োগের আগ্রহ হারাচ্ছেন। কারণ হিসাবে উল্লেখ করছেন-রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির ওপর আস্থাহীনতা। এর প্রমাণও মেলে। ২০১৫ সালটা ছিল রাজনৈতিক সহিংসতার বছর। তাই অর্থ পাচারের পরিমাণও ছিল বেশি। দেশে প্রতিবছর বিনিয়োগ ঘাটতির পরিমাণ ১২ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলার। এ অবস্থার মধ্যে বছরে গড়ে ৮ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়ে যাওয়াটা অর্থনীতির জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর। এই পাচারকৃত অর্থের ঘাটতি পূরণ করতে হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স, বিদেশি ঋণ, বিদেশি বিনিয়োগ, বিদেশি দান-অনুদান এবং বিদেশি সাহায্য ইত্যাদি দিয়ে। এ দুর্ভাবনার বিষয়টি নিয়ে সরকারি মহলের কোনো সুস্পষ্ট উদ্যোগ বা উদ্বেগ আমাদের চোখে পড়েনি। বরং সরকারের উপর মহলের কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের কাছে অর্থ পাচারকারীদের কোনো তালিকা নেই, আপনারা খুঁজে বের করুন। এটি একটি দায়সারা গোছের কথা। তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম এমন কোনো সংস্থার সঙ্গেই আমজনতার পরিচয় নেই। সংস্থাগুলো সরকারি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। সরকার চাইলেই তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছার।
সরকারি মহল থেকে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিলেও কিংবা নিতে না পারলেও এ সময়ে তারা এক ধরনের অস্বস্তিতে পড়েছেন। প্রকৃতির বিচারে যাদের বিশ্বাস নেই, তারা এ ঘটনাকে কাকতালীয় বলতে পারেন। অর্থ পাচারকারীরা উন্নত ও সুখী-সমৃদ্ধ জীবনযাপনের আশায় পাড়ি জমাতে চান উন্নত বিশ্বে। পাচারকৃত অর্থে ‘সুখী জীবনে’র লক্ষ্যস্থল হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলো। সেখানে তারা আবাস তৈরি ও বিনিয়োগে আগ্রহী। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ঘোষণা তাদেরকে সম্পদের বিষয়ে শঙ্কিত করে তুলেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে গত ১০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান ও সাত ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এতে করে পাচারকারীরা আশঙ্কা করছে-যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, এমনকি ইউরোপেও কোনো বাংলাদেশির অবৈধ সম্পদ থাকলে তা বাজেয়াপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাই অর্থ পাচারের জন্য নতুন কোনো দেশের অনুসন্ধানে আছেন তারা। সেক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ দেশ হিসাবে কেউ কেউ সংযুক্ত আরব আমিরাত ও তুরস্কের কথা ভাবছেন বলে গণমাধমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
সবচেয়ে বেশি আতঙ্কে আছেন তারাই, যারা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ায় সম্পদ পাচার করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকগুলো দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা চুক্তিও কার্যকর আছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে দেশগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। যুক্তরাষ্ট্রের জারি করা নিষেধাজ্ঞা কিংবা গ্রেফতারি পরোয়ানা উল্লিখিত দেশগুলোতে কার্যকর হওয়ার বহু নজির অতীতে আছে। বিশেষ করে কানাডার ক্ষেত্রে তা অধিকতর কার্যকর। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কানাডার যে আইনি সমঝোতা আছে, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কানাডায় কার্যকর। তাছাড়া এ ধরনের বিষয়ে ইউরোপের দেশগুলোও যুক্তরাষ্ট্রকে উপেক্ষা করে না। এ বিষয়ে একটি সংবাদমাধ্যম বলছে, ‘যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা অন্য দেশগুলোতে কীভাবে কাজ করে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ের জ্যেষ্ঠ নির্বাহী মেং ওয়ানঝু। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি ইরানের ওপর আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দিয়ে হুয়াওয়ের ব্যবসা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলোকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। এ অভিযোগে তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা হওয়ার পর কানাডা তাকে গ্রেফতার করে। তিন বছর ধরে তিনি কানাডার ভ্যাংকুভারে তার পিতা হুয়াওয়ের প্রতিষ্ঠাতা জেনফেংয়ের মালিকানাধীন একটি বাড়িতে গৃহবন্দি অবস্থায় ছিলেন। এ বছরের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কূটনীতিকদের মধ্যে আলোচনা ও সমঝোতার পর তিনি মুক্তি পান। কানাডায় তার পিতার বিনিয়োগ ও বাড়ি থাকার পরও মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও মামলা থাকার কারণে তাকে আইনি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও দেশের কোনো সম্পদ কানাডায় থাকলে তা বেহাত হওয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়।’ অর্থ পাচারকারীদের অধিকতর ভাবনার বিষয় হলো যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের নিষেধাজ্ঞার পরিধি সম্প্রসারিত করে, তাহলে অনেকেই এর আওতায় এসে যাবেন। তাই নতুন পথের সন্ধানে আছেন তারা।
সুইস ব্যাংকের দেশ সুইজারল্যান্ড এক সময় ছিল অর্থ পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্য। সারা বিশ্ব থেকে কর ফাঁকি ও অবৈধ অর্থ পাচারের টাকা জমা হতো এই সুইস ব্যাংকগুলোতে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তারা কঠোর গোপনীয়তা সংরক্ষণ করত। ব্যাংকগুলোর এ ধরনের প্রশ্রয় নিয়ে সারা বিশ্বে ক্রমাগত সমালোচনা হতে থাকে। ফলে সুইজারল্যান্ড সরকার লেনদেনের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি ও বিধিনিষেধ আরোপ করে। বর্তমান সময়ে ব্যাংকগুলো প্রতিবছরের হিসাব খোলাখুলি প্রকাশ করে। এর বাইরে তারা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অর্থ পাচারের তথ্য আদান-প্রদান করে। তাই অর্থ পাচারকারীদের কাছে সুইজারল্যান্ড এখন আর তেমন আগ্রহের দেশ নয়।
সংযুক্ত আরব আমিরাত ২০১৯ সাল থেকে দেশটিতে বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০ বছরের আবাসিক ভিসা চালু করেছে। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীকে কমপক্ষে ১ কোটি দিরহাম বা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৩ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করতে হবে। আরব আমিরাতের এই সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন বেশ কিছু বাংলাদেশি। অর্থ সরানোর আরেকটি সুযোগ আছে তুরস্কে। ২০১৮ সাল থেকে বিনিয়োগের মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তুরস্ক সরকার। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের মানুষ শুধু আড়াই লাখ ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে তুরস্কের নাগরিক হওয়ার আবেদন করতে পারেন। ভৌগোলিক অবস্থান ও ধর্মীয় রীতি-আচারের কারণে বাংলাদেশিদের জন্য তা আকর্ষণীয় হতে পারে। এক তথ্যে দেখা গেছে, গত তিন বছরে অন্তত ২০০ জন বাংলাদেশি তুরস্কে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন। তারা মূলত ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক। অর্থ পাচারের এসব সম্ভাব্য নতুন গন্তব্য সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে।
অর্থ পাচারকারীরা তাদের পাচারকৃত সম্পদ নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত কিংবা যতটা অস্বস্তিতেই থাকুক না কেন, তাতে আমাদের স্বস্তির কোনো কারণ নেই। দেশের মানুষের কল্যাণে, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বার্থে অর্থ পাচার বন্ধ এবং পাচারকৃত টাকা উদ্ধারে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা আমরা প্রত্যাশা করি। কেননা, নিষেধাজ্ঞার কারণে বাজেয়াপ্ত হওয়া অর্থ উদ্ধার করার কাজটি পাচারকারীদের কাছ থেকে অর্থ উদ্ধারের চেয়ে কঠিন হবে।
মুঈদ রহমান : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়