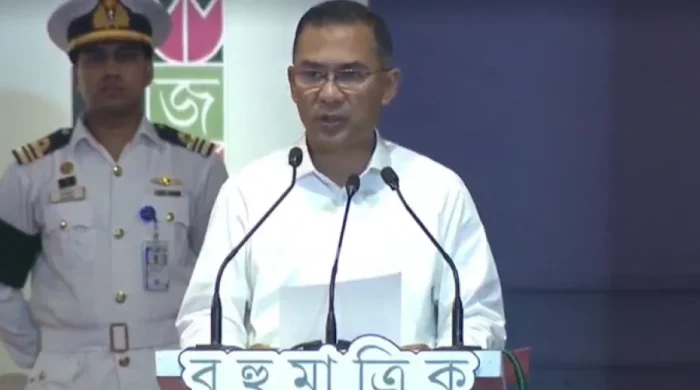সমকালীন শিক্ষা বীক্ষণ ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
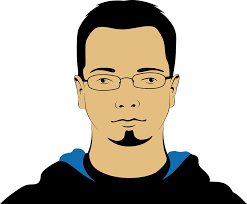
- আপডেট টাইম : সোমবার, ১৮ জুলাই, ২০২২
- ২২২ বার

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও তা টেকসইকরণে প্রধানতম মনোযোগ ও বিনিয়োগের জায়গা হচ্ছে শিক্ষা খাত। শিক্ষা মানুষকে চক্ষুষ্মান করে, দায়িত্বশীল করে, ন্যায়নীতি নির্ভরতার প্রতি অয়োময় প্রত্যয়ী করে, মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ, সমাজ ও অর্থনীতিকে স্বনির্ভর, স্বয়ম্ভর ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে, মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করে, আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত রাখে, সঙ্কট সন্ধিক্ষণে ধীমান পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশ পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধারণে অচল অটল থাকার শক্তি জোগায় যে শিক্ষা, খোদ সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে নানা অন্তর্ঘাতমূলক অবস্থা-ব্যবস্থা করে বিপথগামীকরণে কাছে ও দূরের শত্রুরা তৎপর থাকে, থাকাটাই স্বাভাবিক, কেননা মেধাশূন্য ও মোহগ্রস্ত দেশ ও জাতিকে অন্তঃসারশূন্য করতে, শোষণ ও বঞ্চিত করতে এর চেয়ে মোক্ষম উপায় আর নেই। সহস্র দ্বীপের দেশ সাগর মেখলা জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কিছু নেই বরং নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা।
এসব মোকাবেলা করে জাপান আজ বিশ্বের একটি পরাশক্তি হিসেবে দীপ্যমান, কারণ তাদের আছে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত মানবসম্পদ। সেখানে পরিবার ও প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানো যে, উচ্চতর স্তরে যখনই যতই নয়ছয় চলুক না কেন তাকে প্রতিরোধ করার আত্মশক্তি সেখানে বিদ্যমান। সমাজে আন্তঃসহায়ক সলিলা শক্তির (রেজিলিয়েন্ট পাওয়ার) উদ্ভব, বিকাশ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উজ্জীবিত।
আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিগত এক শতকে এর অনবদ্য ভূমিকা বিশ্লেষণ করলেই তো বোঝা যায়- আত্মশক্তি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা কতখানি। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে কায়েমি স্বার্থবাদীদের বিরোধিতার স্বরূপ বিশ্লেষণে ধরা পড়বে আবহমানকাল থেকে চলে আসা সে ষড়যন্ত্র এখনো বিদ্যমান নানান অবয়বে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ক্রম অধোগতি, ন্যায়নীতি শিক্ষা থেকে পশ্চাৎপদতার আভাস ইঙ্গিতেও বোঝার কথা ভবিষ্যতের জন্য কোন এবং কেমন মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুযোগের কাল অতিক্রম করছে, ইতোমধ্যে দশক দেড় অতিক্রান্ত হয়েছে আর বড়জোর দুই দশক এই সুযোগ বিদ্যমান থাকবে। মানবসম্পদ উন্নয়নের কোন স্তরে আছি আমরা? আমাদের লক্ষ্য কী? এটি ভাববার সময় বা অবসর মিলছে কই?
উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই ভূখণ্ডে, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের আমলে, গোটা সমাজকে ডিভাইড অ্যান্ড রুল অবয়বে অন্ধকারে রাখার অবারিত অপ্রতিরোধ্য অবকাশের মধ্য থেকে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সঠিক পথে আনতে স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আবদুল লতিফ, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, সমস্যার ভেতরে ঢুকে তারা যে অকুতোভয় ভূমিকা পালন করেছিলেন আজ তাদের কথা মনে পড়ে যায়। গত ১০ এবং ১৩ জুলাই ছিল ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী। অন্তত এ অবসরেও তার শিক্ষা ভাবনা ও দর্শন নিয়ে চর্চার মধ্যেও তো মিলতে পারে, পাওয়া যেতে পারে প্রেরণা।
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে সংস্কৃত নিয়ে ১৯০৪ সালে ‘এন্ট্রান্স’ (বর্তমান মাধ্যমিক পরীক্ষা), ১৯০৮-০৯ সাল পর্যন্ত যশোর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা ও ১৯০৯ সালে সংস্কৃতে বিএ (অনার্স), ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এমএ এবং ১৯১৪ সালে এলএলবি পাস করেন। ১৯১৫ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৫-১৯ সালে চব্বিশ পরগনার বশিরহাটে আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন। এ সময় স্থানীয় পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯১৯ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাকে তার সময়ে জানান Shahidullah Bar is not for you. Come to our University. তিনি ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের সহকর্মী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক পদে নিযুক্তিলাভ করেন এবং ১৯২১ সাল অবধি সে দায়িত্ব পালন করেন।
১৯২১ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯২২-২৪ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপনা করেন। ১৯২৬-২৮ পর্যন্ত প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক ভাষা, প্রাচীন পার্সি, তিব্বত, বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষা অধ্যয়ন ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন, উপরন্তু ডিপ্লোফোন সনদপত্র লাভ করেন। ১৯২৭-২৮ এ সরবনে পাঠরত অবস্থাতেই এক অবকাশে জার্মানির ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন। ১৯৩৭ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ পৃথক হলে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও রিডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ এবং ১৯৪৪ সালে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত ওই পদে অধ্যাপনা করেন। অবসর গ্রহণের পরপরই তিনি বগুড়ার আযীযুল হক কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পান। ১৯৫৮ সালে তিনি শিক্ষকতার পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।
মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অন্যতম দিক ছিল, দেশ, সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সক্রিয় সম্পৃক্ততা। তিনি ছাত্রজীবনেই সদ্য প্রতিষ্ঠিত ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’র সম্পাদক (১৯১১-১৫) হন; তিনি দ্বিতীয় দফায় যুগ্ম সম্পাদকের (১৯১৮-২১) দায়িত্ব পালন করেন।
১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা’ নামে একটি ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠনের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন (১৯১৭)। ১৯২৩ এর ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের সমাবর্তন উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। ছিলেন ১৯২৬ এর ১৯ জানুয়ারি ঢাকায় ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ আয়োজিত প্রতিষ্ঠা সভার সভাপতি। ১৯২৮ সালে কলকাতায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুবক সম্মেলনের প্রথম ও ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪১ এ হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে ভাষাতত্ত¡ শাখার সভাপতি ও Philology and Indian Linguistics শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ। ১৯৪২ এ ঢাকায় ‘সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি’ আয়োজিত সোভিয়েত মেলা’ নামে চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তিনি। ১৯৪৮ সালে পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। মাদ্রাজে ‘ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অন ট্র্যাডিশনাল কালচার ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া’ অনুষ্ঠানে তিনি ইউনেস্কোর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তার চেয়ারম্যান মনোনীত হন।
বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ও প্রাচ্যের অন্যতম ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তার শিক্ষাভাবনায় ধর্মীয় অনুভূতি অপেক্ষা জাতীয় অনুভ‚তিকে অধিক গুরুত্ব দেন।
জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে তার বক্তব্য- ‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ রেখে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকার জো-টি নেই।’ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এ দুঃসাহসিক উক্তি বাঙালির জাতীয় চেতনা শাণিতকরণে মাইলফলকের ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পরপরই দেশের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে, না বাংলা হবে এ বিতর্ক সৃষ্টি হলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন তিনি। তার এ ভূমিকার ফলে পূর্ববাংলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
ভাষা আন্দোলনের সময় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে লেখনীর মাধ্যমে ও সভা-সমিতির বক্তৃতায় জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করে আন্দোলনের পথ প্রশস্ত ও গতি বৃদ্ধি করেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে ড. জিয়াউদ্দীন উর্দু ভাষার পক্ষে ওকালতি করলে ড. শহীদুল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর প্রতিবাদ করে বলেন, ‘বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দি ভাষা গ্রহণ করা হইলে, ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন রূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার পক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদ রূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবল বৈজ্ঞানিক শিক্ষনীতির বিরোধীই নহে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতিবিগর্হিতও বটে।’ (পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা, দৈনিক আজাদ, ১২ শ্রাবণ ১৩৫৪)
তিনি একজন সুযোগ্য পণ্ডিত ও অর্ধশতাব্দীকাল শিক্ষক হিসেবে কাটিয়েছেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি অভিজ্ঞতার আলোকে হয়তো এটি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে, যে জাতির শিশুসাহিত্যের গতি গঠনমূলক নয় এবং শিশুশিক্ষার সহকর্মী নয় যে জাতির বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও শিক্ষার প্রসার কোনোমতেই সম্ভব নয়। শিশুর সুশিক্ষা ও তাদের সুকুমারবৃত্তিগুলো বিকশিত হওয়ার মতো ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে না পারলে ভবিষ্যতে কোনো কল্যাণকর কিছু তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। শিশুদের সুকুমারবৃত্তি প্রস্ফুটনের ক্ষেত্র হলো শিশুসাহিত্য। বলা বাহুল্য, আমাদের শিশুসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি।
শিশু-কিশোরদের জন্যে তার সচিত্র মাসিক পত্রিকা ‘আঙুর’-এর কথা অনেকে শুনে থাকবেন। আমাদের তৎকালীন সমাজে এই আঙুরই প্রথম ও একমাত্র কিশোর পত্রিকা। অবশ্য এর আগে ‘সন্দেশ’ ও ‘মৌচাক’ নামে আরো দু’টি কিশোর পত্রিকা ছিল কিন্তু আঙুরের মতো সন্দেশ ও মৌচাক তেমনিভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি কিশোর সমাজকে। যদিও বাংলার আর্দ্র আবহাওয়ায় ‘আঙুর’ বেশি দিন বাঁচেনি (১৩২৭ বাংলা সালের বৈশাখ থেকে ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত)। তবু এ স্বল্প কালকে ‘আঙুর’-এর স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এ পত্রিকাতেই লিখতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, ডাক্তার আবদুল ওয়াহেদ, অধ্যাপক আলী আহমদ প্রমুখ। এই পত্রিকার প্রচ্ছদে থাকত আঙুরের গাছ এবং থলি থলি আঙুর। আঙুরের লোভে ছেলেমেয়েরা চারিদিকে মাতালের মতো ঘোরাফেরা করছে। তিনি ছিলেন ওই পত্রিকার সম্পাদক।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিশাল জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন তা তাকে গোঁড়ামি অথবা অহঙ্কারী করে তোলেনি। বরং এই বিশাল জ্ঞানরাজি তাকে দান করেছিল সুমহান ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু নিজ ধর্ম ইসলাম চর্চা করেননি অথবা আপন ধর্মে নিজেকে সঁপে দিয়ে অন্ধত্ব বরণ করেননি। অপরের ধর্মীয় পুস্তকাবলি পাঠ ও চর্চা করে তিনি দেখিয়ে গেছেন ধর্ম মানুষকে বেঁধে রাখতে পারে না। বরং ধর্ম মানুষকে দিয়েছে মহত্তম মুক্তি। তিনি ছিলেন শিশুর মতো সরল। হিংসা, ঈর্ষা, অহঙ্কার কোনোদিন তার চরিত্রে ঠাঁই পায়নি। তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল শিক্ষকতা করে কাটান। তার এই উজ্জ্বল মানবছায়ায় জ্ঞানের সুশীতল বারিধারা পান করে কতজন যে ধন্য হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।
গবেষণা করে শিক্ষাব্যবস্থায় কিভাবে গতিধারা নির্ধারণ করা যায় সে ব্যাপারে তার ছিল প্রাণান্ত প্রয়াস, তারই ফসল আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়ন, বাংলা বানান রীতির সংস্কার, ভাষা আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চার, বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা সন তারিখ গণনার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রবর্তনের মধ্যে ছিল তার দূরদর্শী মনোযোগ ও অবদান।