নিয়ন্ত্রণ ও কালো আইন
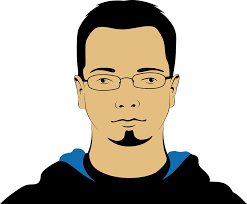
- আপডেট টাইম : মঙ্গলবার, ৩ মার্চ, ২০২০
- ৪৩৭ বার

রিজভী আহমেদ:
নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ববাদী শাসনে নিয়ন্ত্রণই একমাত্র হাতিয়ার শাসকগোষ্ঠীর। মূলত জনগণকে বন্দী করতেই রাষ্ট্রসমাজে সর্বত্র শৃঙ্খলের থাবা অব্যাহত থাকে। সর্বত্র নিয়ন্ত্রণের এক সর্বনাশা বৃত্তে আবদ্ধ থাকে দেশের জনগণ। কর্তৃত্ববাদী শাসকগোষ্ঠীর কাছে ‘জনগণের স্বাধীনতা’ কথাটি ভয়ের। কোনোভাবেই যাতে নাগরিক স্বাধীনতার স্ফুরণ না ঘটে, সেজন্য ক্ষমতাসীনরা নিয়ন্ত্রণের দড়ি হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। আর এ জন্য জনপ্রতিনিধিহীন আইনসভায় প্রণীত হতে থাকে একের পর এক মানুষের ভাষা ও কণ্ঠ রোধের নানা গণবিরোধী আইন। ক’দিন আগে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘আমার ভোটের প্রয়োজন হয় না’। কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বময় একদলীয় ও ম্যান্ডেটবিহীন শাসকদের কথারই প্রতিধ্বনি এটা। যে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, পৃথিবীর স্বেচ্ছাচারী শাসকদের স্বরূপ একই ধরনের। স্থানভেদে তাদের ভাষাও প্রায় একই। তাদের জনগণকে নিঃশর্ত নিয়ন্ত্রণের খাঁচায় আটকে রাখার মূল উদ্দেশ্য হলো- দখলকৃত ক্ষমতা ধরে রাখা এবং রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যথেচ্ছাচার কায়েম করা। এ জন্য তারা সবার অংশগ্রহণে সুষ্ঠু ভোট এবং জবাবদিহিতাকে সহ্য করতে পারে না।
তাই একতরফা জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন করে মিডিয়া ও এনজিও নিয়ন্ত্রণ, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, সরকারি চাকরি আইন ইত্যাদি প্রায় দুই শতাধিক কালো আইন প্রণয়নের অব্যাহত ধারাবাহিকতায় মানুষকে যেন খোঁয়াড়ের প্রাণী বানানো হচ্ছে। বিনাভোটের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদে এসব আইন পাস করার উদ্দেশ্য হলো- সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কেউ যেন নিচুগলায়ও কোনো আওয়াজ করতে না পারে। আর অবৈধ ক্ষমতার চাহিদা মেটাতে জনগণকে দৃঢ় বন্ধনে বন্দী করতেই এসব গণবিরোধী আইন প্রণয়নের প্রয়োজন। মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সর্বশেষ কী শরবিদ্ধ করা হবে তা কেউ জানে না। তবে মানুষ প্রতিনিয়ত এ নিয়ে গভীর শঙ্কায় আছে। নিয়ন্ত্রণমূলক এসব আইন প্রণয়নে সরকারের অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে জ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই। বেপরোয়া দুর্নীতি, অনাচার ও স্বেচ্ছাচারিতাকে নিরাপদ করা, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি লুটপাটের মাধ্যমে সীমাহীন দুর্নীতি, উদ্ধত সন্ত্রাস, বিরোধী দল দমনে নিষ্ঠুর পদ্ধতির প্রয়োগ ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিরোধী দল, গণমাধ্যম, বেসরকারি সংগঠন, ওয়াচডগ ও মানবাধিকার গ্রুপের সমালোচনাকে বন্ধ করতে এসব আইন প্রণীত হয়ে আসছে। ২০১৪ সালে ১৫৪টি আসনে বিনাভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত দশম জাতীয় সংসদ এবং ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ‘নিশিরাতের ভোটে’র সংসদে কোনো কার্যকর বিরোধী দল নেই। সুতরাং এ ধরনের সংসদে যে আইন তৈরি হবে, তা যে মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার আইন হিসেবেই গণ্য হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
জনগণের মত প্রকাশের অধিকারকে আরো খর্ব করার জন্য ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনটি প্রস্তাবের পর এর বিরুদ্ধে গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমের কর্মীরা সোচ্চার হয়েছেন। তারা মনে করেন, গণমাধ্যমকর্মীদের কাজের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করতে এই আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার হবে। এই আইন পাস হওয়ার পর গ্রেফতার ও হয়রানি চলছে ব্যাপকভাবে। এই আইনে সরকারের গোপনীয়তা ভঙ্গ করলে ১৪ বছরের সাজা হবে। অথচ ‘সরকারি গোপনীয়তা’ কী, সে বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই আইনের ৪৩ ধারায় পরোয়ানা ছাড়াই তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেফতারের যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে; তাতে গণমাধ্যমকর্মীরা গভীর সঙ্কটে পড়বেন। ৫৩ ধারায় বলা হয়েছেÑ আইনের ১৪টি ধারা হবে অজামিনযোগ্য।
সুতরাং ব্যক্তির মানবাধিকার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর এটি একটি হুমকি। এ আইনটি প্রণয়নের মাধ্যমে গণমাধ্যম ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সরকারের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হবে। এই আইন যে সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক দমননীতির অংশ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ‘অশোভন-অশালীন’ বক্তব্যের নামে যে কাউকে ধরা সম্ভব। ‘বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি আইনে’র ৫৭ ধারা বাতিলের পক্ষে জনমত ফুঁসে উঠলেও সেই ধারার আদলে প্রণীত, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারাসহ বিভিন্ন ধারায় তা ভাগ করে দেয়া হয়েছে। ৩২ ধারা সাংবাদিকদের জন্য বিপজ্জনক। তাদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সরকারের বিরুদ্ধে গেলে তারা হয়রানির শিকার হতে পারেন। ৪৩ ধারা অনুযায়ী, পুলিশ মনে করলে যে কাউকে গ্রেফতার বা যেকোনো কিছু জব্দ করতে পারবে।
২০০৬ সালের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০১৩ সালে সংশোধন করে গণবিরোধী ৫৭ ধারা যুক্ত করা হয়। জনরোষের ভয়ে ৫৭ ধারায় আলোাচিত ‘মানহানি’, ‘মিথ্যা-অশ্লীল’, ‘আইনশৃঙ্খলার অবনতি’ ও ‘ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত’সহ বিভিন্ন বিষয় ডিজিটাল আইনের বিভিন্ন ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আইনের বিষয়বস্তু এবং অপারেশনালের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ ও শাস্তির ব্যাপক অপপ্রয়োগ হওয়া সম্ভব। বাকস্বাধীনতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি অধিকার। সেটা এই আইন দিয়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করার সুযোগ থাকবে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিধান রেখে (বৈদেশিক অনুদান স্বেচ্ছাসেবকমূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল-২০১৬ প্রণীত হয়েছে। এই বিলে কোনো এনজিও বা এনজিও কর্মকর্তা সংবিধান বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে অশোভন মন্তব্য করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। অনেকের মতে, এ আইনটি করা হয়েছে ভস্মীভূত গণতন্ত্রের ছাইকেও বাতাসে উড়িয়ে দিতে, যাতে কোনো চিহ্ন না থাকে। এটা গভীর দুরভিসন্ধিমূলক, যা আজ সর্বসাধারণের কাছে সুস্পষ্ট।
সরকারি চাকরি আইন-২০১৮ প্রণয়নের ফলে একদলীয় রাজত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে। কারণ, জনগণের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিরাপদ করতে আজ্ঞাবাহী প্রশাসন অপরিহার্য। তাই সরকারি কর্মকর্তাদের অনুগত রাখতে তাদের ইনসেন্টিভ দেয়া হয়েছে সরকারি চাকরি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। এই আইনে সরকারি কোনো কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সাথে সম্পর্কিত অভিযোগে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক অভিযোগপত্র গৃহীত হওয়ার আগে তাকে গ্রেফতার করতে হলে, সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।
২০০৯ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরপরই সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ইনডেমনিটি আইন প্রণয়ন করেছিল। বলা হয়েছিল- দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যই এ আইন। কিন্তু এ আইনটি ‘সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক’ বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন। তাদের মতে, বিদ্যুৎ খাতে হরিলুটের আইনি মোড়ক দেয়ার জন্যই এ আইনটি করা হয়েছিল। এটি এখন সুস্পষ্ট যে, ঘনিষ্ঠজনদের সুবিধা দিতেই আইনটি তৈরি করা হয়েছে।
‘তথ্য অধিকার আইন-২০০৯’ এ বাকস্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার এই অধ্যাদেশের লক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৭৬৬ সালে প্রথম সুইডেনে এ ধরনের আইন প্রবর্তিত হয়েছিল, যা ‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইন’ নামে পরিচিতি। তথ্য অধিকারসংক্রান্ত আইন প্রাচীনতম আইন হিসেবে সাধারণভাবে স্বীকৃত। কিন্তু বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী, দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনসংক্রান্ত তথ্য জানার আইনে অধিকার থাকলেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাসের ফলে এই সুবিধা সার্বিকভাবে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন সুরক্ষিত হয়ে অপরাধের বিস্তার ঘটছে। এ আইনটি মূলত কালো আইনগুলোর মুখে মানবাধিকারের মুখোশ ছাড়া আর কিছু নয়।
জনগণের গলা টিপে ধরার জন্যই একের পর এক কালো আইনের রেকর্ড গড়েছে সরকার। এমন আইন দুঃশাসনের তামসিক প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। কালো আইন দিয়ে দেশের জনগণ সাব-হিউম্যানে পরিণত হয়। সরকারের বিরুদ্ধে টুঁ-শব্দ হলেই তাদের শিরদাঁড়া দিয়ে হিমশীতল রক্ত বইতে থাকে। কালো আইনে মানুষের অস্তিত্বের স্বাধীনতা ও উদ্ভাবনী শক্তি অপহৃত হয়। তাই মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ, কণ্ঠ রোধ, গণতন্ত্রে স্বীকৃত বিরোধী দলের কার্যক্রম সঙ্কুুচিত করা এবং রাষ্ট্রীয় অর্থের লুটপাট করার জন্য ধারাবাহিকভাবে গণবিরোধী আইনের যাঁতাকলে জনগণ আজ পিষ্ট হচ্ছে। কালো আইন নিবর্তনমূলক রাষ্ট্রের নমুনা। জনসাধারণের প্রতিবাদে রাষ্ট্র আরো হিংস্র হয়ে ওঠে। তাই কালো আইনের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে ক্ষমতাসীনদের। গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদের জলাঞ্জলি দিতেই এ ধরনের আইন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।
লেখক : সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব, বিএনপি


























