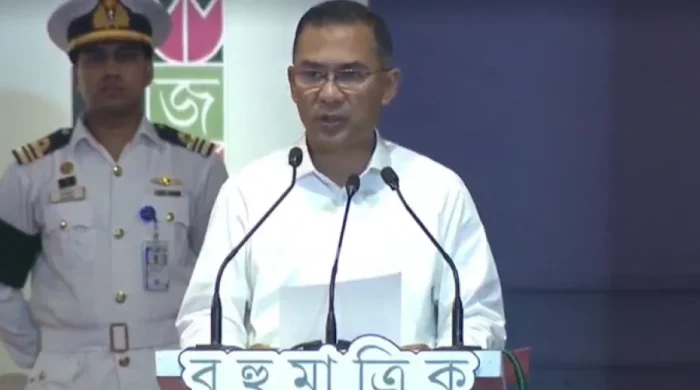বিদ্যাসাগরের মুখোমুখি!
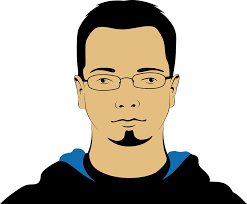
- আপডেট টাইম : মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই, ২০২০
- ৩৫৪ বার

‘বিদ্যাসাগর, আপনি আমাদের প্রণম্য, তবু আপনাকে নিয়ে আমরা বেশ ভয়ে ভয়ে থাকি। হ্যাঁ, আমরা জানি, যতই আমরা আপনার মূর্তির মাথা ভাঙি বা নতুন মূর্তি বসাই, বা আপনার নামে সেতু করি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় করি, তাতে আপনার কিছু এসে যায় না। আপনি যা ছিলেন আপনি তা-ই থাকবেন। কোথায় থাকবেন, কার কাছে? আমাদের স্মৃতির কুলুঙ্গিতে, দ্বিশত জন্মবার্ষিকীর ধুপধুনোয় আচ্ছন্ন হয়ে হাঁচি-কাশিতে বিপর্যস্ত, নাকি মুদ্রিত গ্রন্থে মলাটবদ্ধ ও দূরবর্তী, যা আমরা খেরোর কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখব। আপনিই বলে দিন, আপনাকে নিয়ে আমরা কী করব।’
সেই অগ্নিচক্ষু ব্রাহ্মণের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলাম আমি। তিনি কোমল স্বরে বললেন, ‘আগে বল্, আমাকে নিয়ে এখন তোরা কী ভাবছিস।’
আমি বললাম, ‘অন্যেরা কে কী ভাবে জানি না, আমি এটা ভেবে অবাক হয়ে যাই যে, মেদিনীপুরের এক এঁদো গ্রামের ছেলে আপনি, আপনার বাপ-ঠাকুরদারা কেউ বড় বা বিখ্যাত লোক ছিলেন না, গরিবস্য গরিব, আধুনিক শিক্ষাহীন, তবু আপনি আপনার জীবনে কী করে এমন উঁচুতে উঠলেন যে বলতে পারলেন, এ দেশে এমন বড়লোক নেই যার নাকের সামনে এই চটিজুতো না নাচাতে পারি। আপনি বেঁটেখাটো মানুষ, কিন্তু আপনার মাথা সবার মাথা ছাড়িয়ে উঠল কেমন করে? শুধু অপরিমিত মেধার জোরে? ‘বিদ্যাসাগর’ পদবি তো সংস্কৃত কলেজে কত ছাত্রই পেয়েছিল?’
বিদ্যাসাগর বললেন, ‘মেধা-টেধা শুধু নয় রে। আমার একটা প্রচণ্ড জেদ ছিল। পড়াশুনোটাও আমার একটা জেদ। এটা অনেকটা আমার একার লড়াই, সে আমি লড়ব। এটা হয়তো আমার বাপ-ঠাকুরদার ধারা। আমার ঠাকুরদা ডাকাতদের পিটিয়েছিলেন আর ভালুকের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন জানিস তো! বাবা যখন ১৮২৮ সালে আমাকে কলকাতা নিয়ে এলেন তখনই আমার মনে হল, ওরে ঈশ্বর, তুই রাজধানীতে এসেছিস, তার মানে এখন তুই আর সেই পাড়াগাঁর বাসিন্দে নোস, তুই সারা পৃথিবীর নাগরিক। তোকে একটা কোথাও পৌঁছতে হবে। শুধু তোর নিজের জন্য নয়। তোর বাবা না-খেয়ে, আধপেটা খেয়ে তোকে মানুষ করতে কলকাতায় এনেছেন, তোর মা-ঠাকুমা গ্রামে বসে তোর জন্যে চোখের জল ফেলে, তাদের মুখ রাখতে হবে।’
‘‘এই জেদটারই অন্য চেহারা হল তো ‘দুর্জয় সাহস’, রবীন্দ্রনাথ যে কথাটা বলেছেন, বলেছেন যেটা আপনার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য’’, আমি বললাম। ‘এই সাহস কি আজ আমরা কেউ দেখাতে পারি? আমাদের কত ভয়, কত লোভ। বিশ্বায়ন এসে আমাদের জেদের শেকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলেছে মনে হয়। কোটি কোটি টাকার হাতবদল হচ্ছে, দলবদল হচ্ছে, ঘুষ, তোলা কাটমানিতে ছয়লাব দেশ। আমাদের জেদের আর সাহসের শিরাটা কেউ যেন কেটে নিয়ে গেছে। আমরা কী করব আপনাকে নিয়ে?’
বিদ্যাসাগর এবার ধমকে উঠলেন। ‘হতভাগারা, আমি বলে দেব, সেই আশায় তোরা বসে আছিস! জেদ আর সাহস ধার করা যায় নাকি একধামা চালের মতো, টাকার মতো! নিজেদের ভেতর থেকে যদি জেদ আর সাহস উদ্ধার করতে না পারিস তো যা মরগে যা!’
আমি হাল ছাড়লাম না। বলতে লাগলাম, ১৮৪১-এ আপনি বিদ্যাসাগর হয়ে বেরোলেন, বলুন তো কী করে তখন বাংলার সমাজের সেই যে এলিটস্য এলিট, সেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নজরে পড়লেন? গাঁয়ের ছেলে এতটা সিঁড়ি ভাঙল কী করে? এটাও আমাদের কাছে একটা অদ্ভুত ব্যাপার!’
‘‘সেটা বোধহয় একটু-আধটু বাংলা লিখতে পারতুম বলে। ঠাকুরমশায় তখন ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা বার করছেন, অক্ষয়কুমার দত্ত আর আমাকে তার কাজে লাগিয়ে দিলেন। অক্ষয়ও বেশ ভালো বাংলা লিখত। তোদের এখনকার তুলনায় আমাদের বাংলা একটু খটোমটো মনে হবে; কিন্তু তখন ওইটেই ছিল চল।’’
‘এখানেও আমার আশ্চর্য লাগে যে, দেবেন্দ্রনাথের কাছে গিয়েও আপনি ব্রাহ্ম হলেন না। আসলে আপনি কী ধর্ম মানতেন তা নিয়ে বাঙালি খুব ধাঁধায় আছে।’
বিদ্যাসাগর খানিকটা ‘হ্যা-হ্যা’ করে হাসলেন, যেন বিষয়টায় দারুণ মজা পেয়েছেন। বললেন, ‘হ্যাঁ, এখন ধম্মো ধম্মো করে হদ্দ হয়ে গেলি তোরা। ঠাকুরে ঠাকুরে গুরুদেবে গুরুদেবে জ্যোতিষে আংটিতে পাথরে তাগায় ধুন্ধুমার। বাপের জন্মে শুনিনি বাঙালি গণেশের বারোয়ারি করছে। এখন পুজোর আগে খুঁটিও হয়েছে তোদের এক ঠাকুর, তারও পুজো কচ্চিস। আর একদল হতভাগা ধর্মে ধর্মে লড়াই বাধিয়ে মজা লুটতে চাইছে!’
‘কিন্তু আপনার ধর্ম?’ আমার নাছোড়বান্দা প্রশ্ন।
‘আমার আবার ধর্ম কী? আমার ধর্ম মানুষ! হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খেরেস্তান ওসব কিছু নয়, শুধু মানুষ। আমি নেহাত পইতে ছাড়তে পারিনি, কিন্তু বাড়িতে পুজো-আচ্চার ধার-ধারিনি। ছেলেবেলার পর সন্ধ্যাআহ্নিকও ছেড়ে দিয়েছিলুম। গুরুমন্ত্র নিইনি, তেত্থ-মেত্থ কিচ্ছু করিনি। কাশীতে গেছি বাবা-মাকে দেখতে বিশ্বনাথের মন্দিরমুখো হইনি। পাণ্ডারা এসে অভিযোগ করায় বাবা-মাকে দেখিয়ে বলেছি, এই আমার বাবা বিশ্বনাথ, এই আমার মা অন্নপূর্ণা। ছাড়্ ওসব কথা!’
বলে আবার ‘হ্যা হ্যা’ করে হাসলেন কিছুক্ষণ। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, ‘জীবনে আমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভক্তি করতুম সেই আমার মায়েরও তেমন ধর্মের বাই ছিল না। একবার বাবা বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো করতে চাইলেন তো মা বললেন, তো ওই খরচে গাঁয়ের গরিবদের কম্বল দেওয়া হোক, পুজোয় কাজ নেই।’
আমি আরও বললাম, ‘‘দেখি যে আপনার পড়ার সিলেবাসে কোথাও বিজ্ঞান ছিল না, কিন্তু আপনি ‘বোধোদয়’ হোক, ‘জীবন চরিত’ হোক, সব জায়গায় বিজ্ঞানের কথা লিখেছেন, গ্যালিলেও, কোপার্নিকাস, নিউটন এই সব বিজ্ঞানীর জীবনী লিখেছেন। ধর্মগুরুদের ত্রিসীমানায় হাঁটেননি। এটা কেন করলেন?’’
বিদ্যাসাগর আবার মিটিমিটি হাসতে লাগলেন, কোনো উত্তর দিলেন না।
আমি বললাম, ‘কিন্তু আপনার দয়া আর দানধ্যান? সে কথা তো এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে!’
বিদ্যাসাগর জিভ কেটে কানে আঙুল দিলেন। বললেন, ‘ছিঃ ছিঃ, ওসব আমার শুনতে নেই। মানুষকে ভালোবাসতাম, আমার মা যেমন বাসতেন, তাই লোকের কষ্ট দেখলে অস্থির লাগত। তা সে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোরা মানুষকে সাহায্য করবি কিনা সে কি আমি বলে দেব? না আমার জন্মের দুশ’ বছর পড়লে সক্কালবেলায় সংকল্প নিবি যে, না, বিদ্যাসাগর করে গেছে তাই গরিব আর দুঃখী মানুষকে সেবা করতে হবে! মেয়েরা তো আমাদের সমাজে আরও দুঃখী ছিল- বেধবারা, সেই মেয়েরা, যাদের বাচ্চা বয়সে বে দেওয়া হতো। তা তাদের কথা যে ভাববে নে সে মানুষ নাকি?’
আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আর শিক্ষা?’
বিদ্যাসাগর বললেন, ‘‘শিক্ষা কী? কথাটা পরিষ্কার করে বলবি তো? দ্যাখ্, আমার সময়ে সবাই বুঝেছিল, ওই তোরা যাকে আজকাল ‘ক্ষমতায়ন’ না কী বলিস, তার প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষা। বড়লোকদের চেয়ে গরিবদের তা অনেক বেশি দরকার, মেয়েদের তা অনেক বেশি দরকার। তাই, শুধু বেধবার বে নয়, তার আগেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম মেয়েদের শিক্ষায়, পরে মেট্রপলিটান শুদ্ধ এখানে-ওখানে গাদা গাদা ইশকুল বসালুম। কী করতে? শিক্ষা পেলে ছেলে মেয়ে দুয়েরই লাভ হবে। ‘বর্ণপরিচয়’ লিখলুম। কে একজন পণ্ডিত নাকি বলেছে আমি ব্রিটিশ রাজের জন্যে সুবোধ প্রজা তৈরি করার জন্যে লিখেছি। মিথ্যে কথা। কলকাতার বড়লোকের ছেলেরা সব বখে যাচ্ছিল, মাইকেলের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’, দীনবন্ধুর ‘সধবার একাদশী’ পড়েছিস তো! তাই ভালো ছেলের একটা আদল দিতে চাইছিলুম।’’
আমি বললুম, ‘আপনি নিজে তো মোটেই আপনার গোপালের মতো ভালো ছেলে ছিলেন না!’
বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, ‘তবেই বোঝ্! আমার লেখা আর আমার জীবন- দুটোই তোদের পড়তে হবে, তোদের রবিঠাকুর যা করেছিল।’
বিদ্যাসাগর বললেন, ‘ওই সময়ে সমাজে, শিক্ষায়, কতকগুলো কাজের দরকার ছিল। শুধু আমি কেন, অনেকেই এগিয়ে এসেছিল। এখন তোদের হাজার হাজার ইশকুল-কলেজ হয়েছে, শুধু মেয়েদের কত বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। কিন্তু পড়তে গেলে হাজার হাজার টাকা লাগছে। হ্যাঁ রে, দেশের সব লোক কি বড়লোক হয়ে গেছে? আর কে কী শিখছে তা যাচাই করেছিস?’
আমি কথা ঘোরানোর জন্য বললাম, ‘আর আপনার লেখা বই? কত কত লেখা! আপনি সাহিত্যের গদ্য তৈরি করে দিলেন!’
বিদ্যাসাগর বললেন, ‘সে তোরা পণ্ডিতেরা বলবি ভাষা নিয়ে ছাইভস্ম কী করেছি। তবে আমিই তো শেষ কথা না, পরে কত বড় বড় লেখক হয়েছে বাংলায়। তাই তো হয়!’
আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করাতে বিদ্যাসাগর বেশ ঘাবড়ে গেলেন মনে হল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘‘আচ্ছা, আপনাকে নিয়ে এত গল্প তৈরি হল কেন? উনিশ শতকের আর কোনো মহাপুরুষকে নিয়ে তো এত গল্প হয়নি! এমনকি ভুলভাল গল্প! আপনার জীবনীকাররা বলেছেন যে আপনি দামোদর সাঁতরে পার হননি, কিন্তু লোকে গল্প বানিয়েছে। আপনি ‘নীলদর্পণ’ নাটক দেখতে গিয়ে অত্যাচারী রোগ্সাহেবের অভিনেতার দিকে রেগে চটি ছুড়ে মারেননি, তবু লোকে বানিয়েছে এ গল্প। কত কত গল্প!’’
বিদ্যাসাগর একটু থমকে থেকে কেমন যেন ভিজে স্বরে বললেন, ‘দ্যাখ্, আমাকে যে বাংলার একেবারে মাটির কাছের মানুষেরা ভালোবেসেছিল, এই গল্পগুলো তার প্রমাণ। তারা আমাকে ভালোবেসেছে বলে ভেবেছে, এটা বিদ্যেসাগর করতে পারে, বিদ্যেসাগরই করতে পারে, আর কেউ না।’ বলে একটু কেমন হাসলেন, বললেন, ‘‘এইখানে আমি সকলকে টেক্কা দিয়েছি। ওই তোরা আজকাল যাকে ‘লোকসংস্কৃতি’ না কী বলিস, আমি তার মধ্যে ঢুকে গিয়েছি। সে ওই তলার মানুষেরা আমাকে ভালোবেসেছে বলে।’’
আমি বললাম, ‘আর শেষে আপনার একা হয়ে যাওয়া? তা কেন হল? তলার মানুষের ভালোবাসা তো আপনাকে রক্ষা করতে পারল না। কলকাতা ছেড়ে সতেরো বছর কার্মাটাঁড়ে নির্বাসনে কাটানো?’
বিদ্যাসাগর একটু সময় নিলেন উত্তর দিতে। বললেন, ‘নিজের সত্যকে বুকে নিয়ে তুই সময়ের বিরুদ্ধে যা, সকলের বিরুদ্ধে যা, প্রচলনের বিরুদ্ধে যা, তোকেও একা হতে হবে। আমাকে তো মেরে ফেলারও চেষ্টা হয়েছে! তাতে কী হল? হাল ছেড়ে দিবি নাকি? তা হলে আমার দুশ’ বছর মেনে তোদের কাজ নেই বাপু।’
শেষে যেন একটু ব্যাখ্যা করলেন, ‘আমার জন্য দয়া করে তলার মানুষেরা আমাকে ত্যাগ করেনি। কার্মাটাঁড়ে গিয়ে সাঁওতালদের মধ্যে আমি সুখেই ছিলুম। আমি ঘেন্নায় ছেড়ে গেছি কলকাতার বাবুদের, তাদের মতো অসার আর অপদার্থ দল আমি জন্মে দেখিনি। এদের ওপর ভরসা করেই আমি ডুবেছিলুম।’
তারপর বললেন, ‘তবু আমার কোনো দুঃখু নেই রে। আমি যা সার বুঝেছি, তার জন্যে লড়াইয়ে নেবেছি। একা হয়েও লড়াই ছাড়িনি। সব লড়াই জিতিনি। কিন্তু যারা বাবু নয় তাদের ভালোবাসা তো পেয়েছি! তাই বা কয়জন পায়!’
আমি আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করলাম না। প্রণাম করে চলে এলাম।
পবিত্র সরকার : সাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা