ছোট দেশের বড় কাজ
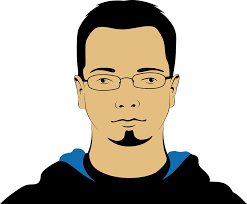
- আপডেট টাইম : শনিবার, ১ ফেব্রুয়ারী, ২০২০
- ৫১৪ বার

এ কে এম মাকসুদুল হক:
গত ২৩ জানুয়ারি ‘আইসিজে’ (International Court of Justice) রোহিঙ্গা সমস্যাসংক্রান্ত এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছেন। এই রায় ভূলুণ্ঠিত মানবতার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। একটি জাতিগোষ্ঠীকে অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে তুলে এনে তাদের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এই মানবিক রায়ের মাধ্যমে। রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর পশুসুলভ বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়। নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মতো পাশবিক অত্যাচারে ভিটেমাটি থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়ে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে রোহিঙ্গা নামের মানুষেরা। এ ধরনের জাতিগত নির্মূল অভিযান থেকে রোহিঙ্গাদের রক্ষার জন্যই মূলত এই রায়।
মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে প্রায় ২০ লাখ রোহিঙ্গা (১৯৮৩ সালের আদমশুমারি মোতাবেক) জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল, যার বেশির ভাগই মুসলমান। মূলত আরব ব্যবসায়ীদের উত্তরসূরি এই জনগোষ্ঠী এ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছিল। তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। মিয়ানমার সরকার তাদের ‘বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী’ বলে অভিযোগ করে এবং তাদের বাংলাদেশে পুশইন করার অজুহাত খুঁজতে থাকে। এরই মাঝে সত্তরের দশক থেকে বিভিন্ন সময় তারা নির্যাতনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকদের চোরাগোপ্তা পথে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়। ১৯৯২ সালে এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি রোহিঙ্গাদের ঢল নেমেছিল আমাদের দেশে। এভাবে প্রায় তিন লাখ রোহিঙ্গা আগেই পালিয়ে এসেছিল।
ইতোমধ্যে মিয়ানমার সরকার রাখাইন অঞ্চলকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনায় আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র চীনেরও জড়িত থাকার কথা জানা যায়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসবাস মিয়ানমার ও চীনের এই বাণিজ্যিক উদ্যোগের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মিলিশিয়া গ্রুপ ‘আরসা’ (আরাকান রোহিঙ্গা শ্যালভেশন আর্মি) রাখাইনের ৩০টিরও বেশি পুলিশ চৌকিতে হামলা করে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অবশ্য ওই আক্রমণের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু এই আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ২৫ আগস্ট থেকেই মিয়ানমার সেনাবাহিনী এবং উগ্রবাদী বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাখাইনের রোহিঙ্গাদের ওপর। ওই আক্রমণে উত্তর রাখাইনের কমপক্ষে ২৮৮টি গ্রাম পুরোপুরি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এতে কমপক্ষে ৭৩০ জন পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুসহ প্রায় ৬৭০০ রোহিঙ্গা নৃশংসভাবে নিহত হয় (বিবিসি নিউজ ২৩/১০/১৯)। সেই সাথে আক্রমণকারী সৈনিকরা রোহিঙ্গা নারী ও বালিকাদের গণধর্ষণে লিপ্ত হয়। এই বর্বরোচিত নির্যাতন থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়ে প্রায় সাড়ে সাত লাখ রোহিঙ্গা কোনো মতে পালিয়ে ছুটে আসে বাংলাদেশে। নৌকায় করে পালিয়ে আসার সময় আরো প্রায় শত লোকের সলিল সমাধি হয় বঙ্গোপসাগরে। সামরিক বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য তারা বাজি রেখে যে যেভাবে পেরেছে পালিয়ে বাংলাদেশের টেকনাফে এসে পৌঁছে। জাতিসঙ্ঘের ভাষায় এই বর্বরতা হলো ‘Textbook example of ethnic cleansing’।
বাংলাদেশের আশ্রয়শিবিরে বর্তমানে প্রায় ১৩ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করছে। কক্সবাজার জেলার প্রায় ১৩টি স্থানে তারা বিভিন্ন শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করছে। মিয়ানমার সেনা অভিযানের শিকার হয়ে যখন তারা বাঁচার আকুতি নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছিল তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এ দেশের ভূমিতে। তাদের তখন আশ্রয় না দিলে হয়তো বা পুরো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীই জাতিগতভাবে নির্মূল হয়ে যেত। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর সেই সময়কার সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত মানবিক ও বিজ্ঞোচিত। বাংলাদেশ সরকার সেই সময় আরো একটি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল। রোহিঙ্গা নিধনের অপরাধ আড়াল করার জন্য মিয়ানমার বাংলাদেশকে সংঘর্ষে জড়ানোর জন্য চেষ্টা চালিয়েছে নির্লজ্জভাবে। তাদের হেলিকপ্টার বারবার আমাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে মিয়ানমারের এই পাতানো খেলা ও উসকানিমূলক ফাঁদ থেকে দূরে সরে রয়েছে। সেই দিনগুলোতে যদি আমাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রতিক্রিয়া দেখাত তাহলে হয়তো ‘আইসিজে’ একটি মানবিক রায় দিয়ে রোহিঙ্গাদের সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত করার সুযোগ পেত না।
অনেকের মতে, ১৩ লাখ রোহিঙ্গা এখন আমাদের জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ আমাদের মাতৃভূমি। তার ওপর আরো ১৩ লাখ মানুষের অতিরিক্ত চাপ আমাদের সহ্য করতে হচ্ছে। বিশাল এই অতিরিক্ত জনগোষ্ঠী আমাদের দেশে নিত্যনতুন আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে। ওদের বসতি স্থাপনের জন্য কক্সবাজার এলাকার বন উজাড় করায় পরিবেশ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। জঙ্গল পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে বাড়িঘর তৈরি এবং রান্নাবান্নার কাজ সবকিছুতেই আমাদের স্বল্প বনভূমির ওপর চাপ পড়ছে। নিত্যপণ্যের মূল্য কক্সবাজার এলাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়তি এই লোকজনের উপস্থিতি আমাদের পর্যটন শিল্পেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই জনগোষ্ঠীর না আছে কোনো শিক্ষা বা না আছে কোনো কারিগরি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা।
বেশির ভাগই রাখাইনের গ্রামাঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের লোক। তদুপরি তাদের অর্ধেকেরও বেশি মহিলা ও শিশু। কাজেই এদের কেন্দ্র করে নানা ধরনের মতলববাজ চক্র তৎপর হয়ে উঠেছে। ‘মাদক ও অস্ত্র চোরাকারবারি, নারী পাচারকারী এবং মানব পাচারকারী চক্রগুলোর আনাগোনার প্রভাবে সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক সমস্যা; যা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর বাড়তি চাপ বৈকি। ইতোমধ্যে ওদের নিজেদের মধ্যে মারামারি করে হতাহতের ঘটনাও ঘটছে। অন্য দিকে, অনেকেই ধরা পড়লেও বেশ কিছু রোহিঙ্গা আমাদের মূল জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে যাচ্ছে। এমনকি দালালের মাধ্যমে অনেক রোহিঙ্গা বাংলাদেশী পাসপোর্ট সংগ্রহ করতেও সক্ষম হয়েছে। মিয়ানমার সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ ‘ইয়াবা’ ট্যাবলেট আসছে; যার বেশির ভাগেরই বাহক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্য। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা এই জনগোষ্ঠীকে ক্যাম্পে বসিয়ে বসিয়ে ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করায় সমস্যা আরো প্রকট হচ্ছে। তাদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে অনীহা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় পাঁচ লাখ শিশুও রয়েছে। এসব শিশুর বেশির ভাগই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তিন বছর ধরে। এভাবে বেড়ে উঠলে এরা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হতে পারে।
সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে উঠতে পারে এই জনগোষ্ঠী। এমনিতেই তাদের শিশু-কিশোররা মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও উগ্র বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর যে ভয়াবহ নৃশংসতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা তাদের ‘রেডিক্যালাইজড’ করার জন্য যথেষ্ট।
যে সন্তানটি চোখের সামনে পিতাকে নিহত এবং মা ও বোনকে সেনাবাহিনীর দ্বারা নির্যাতিত হতে দেখেছে, সে তো ‘আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত অঙ্গার’ হয়ে রয়েছে। এদের যেকোনো সন্ত্রাসী বা উগ্রবাদী গ্রুপ মগজ ধোলাই করে দিতে পারে। উল্লেখ্য, তাদের বেশির ভাগেরই ধর্মের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। কাজেই তাদের উগ্রবাদীতে রূপান্তরিত করা সহজ। এ দিকে, রাখাইনে ‘আরসা’ অনেক আগে থেকেই তৎপর রয়েছে বলে জানা যায়। এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে অসংখ্য দুর্ধর্ষ উগ্রবাদী সংগঠন রয়েছে। নিগৃহীত রোহিঙ্গাদের সাথে ওইসব দলের যোগাযোগ স্থাপিত হলে বিশ্বের শান্তি হুমকির মুখে পড়তে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত করার ফলে পুরো মধ্যপ্রাচ্য এবং আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত সারা বিশ্ব অনিরাপদ হয়ে আছে। তেমনি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নতুন ফিলিস্তিনের সৃষ্টি হতে পারে। এর মাশুল তখন সারা বিশ্বকেই দিতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়।
ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আমাদের এই মহাবিপদের দিনে বাংলাদেশ সবচেয়ে কাছের বন্ধু রাষ্ট্রের কাউকেই পায়নি, বরং তারা নির্লজ্জভাবে মিয়ানমারকেই সমর্থন করে যাচ্ছে। ভারত আমাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে অভিহিত। ভারতের কর্তাব্যক্তিরা কথায় কথায় বলেন যে, প্রতিবেশীই প্রথম আর প্রতিবেশীদের মধ্যে বাংলাদেশই তাদের কাছে প্রথম। কিন্তু রোহিঙ্গা সমস্যার ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় এই প্রতিবেশীকে পাশে পাওয়া যায়নি; বরং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘটনার পর মিয়ানমার সফরে গিয়ে শুধু ‘আরসা’কেই দোষারোপ করে ফিরে এসেছেন। আর আমাদের তারা বরাবরের মতো শুধু ‘লিপ সার্ভিস’ দিয়েছেন, সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন। চীন আমাদের আরেক বন্ধু রাষ্ট্র। সেই চীন আমাদের তো সমর্থন করেইনি, বরং নগ্নভাবে মিয়ানমারের গণহত্যাকে সমর্থন দিয়েছে এবং মিয়ানমারকে এই বিপদ থেকে রক্ষার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এমনকি দু-দু’বার নিরাপত্তা পরিষদে এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাবের প্রতিকূলে ভেটো দেয়।
আমাদের সাথে চীনের বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বর্তমান সরকারের সময় এই সম্পর্ক আরো অনেক বেড়েছে। কিন্তু ২৩ জানুয়ারি ‘আইসিজে’-এর আন্তর্বর্তীকালীন রায় দেয়ার আগেই চীনের প্রেসিডেন্ট ‘শি জিনপিং’ মিয়ানমার সফর করে তাদের সাথে ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে উত্তর রাখাইনের ‘কাইউকপিউ’তে গভীর সমুদ্রবন্দর এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের চুক্তিসহ বিশাল অবকাঠামোগত উন্নয়নের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে গেছেন। ২০১৯ সালে চীন মিয়ানমারে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগকারী দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, যার অবস্থান সিঙ্গাপুরের পরই। আসলে আদর্শিকভাবেই চীন মুসলিমবিরোধী অবস্থানে রয়েছে।
চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলমানদের ওপর নির্যাতনকেও রোহিঙ্গা ইস্যুর সাথে তুলনা করা চলে। কাজেই চীন মিয়ানমারকে রক্ষা করার জন্য এই রোহিঙ্গা সমস্যাটি আন্তর্জাতিকীকরণ না করে বরং বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ‘দ্বিপক্ষীয়’ সমস্যা হিসেবে গণ্য করার জন্য পরামর্শ দিয়ে এসেছে। ফলে প্রায় তিন বছর হতে চললেও এই সমস্যার সামান্য সুরাহা করাও সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে। আমাদের আরেক বন্ধুরাষ্ট্র রাশিয়াও এই বিপদে মিয়ানমারের পাশে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া মিয়ানমারে অস্ত্রের বড় বিক্রেতা এবং সামরিক প্রশিক্ষণদাতা। কাজেই তাদের কাছে একটি নিরপরাধ ও বিশাল জনগোষ্ঠীর নির্মূল হয়ে যাওয়াও বড় বিষয় নয়; বরং অর্থনৈতিক লাভই তাদের কাছে বেশি জরুরি।
নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের ঢল যখন ১৩ লাখে পরিণত হলো তখন পশ্চিমা দেশগুলোসহ সারা বিশ্বে নিন্দার ঝড় ওঠে। শুধু ভারত, চীন ও রাশিয়া নিন্দা জানানো থেকে বিরত রইল। বিশেষ করে চীন ও রাশিয়া মিয়ানমার সরকারের পাশে এসে শক্তভাবে দাঁড়ায়। অপর দিকে, পশ্চিমা দেশগুলোর বিভিন্ন কর্তাব্যক্তি এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নীতিনির্ধারকরা কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের দলে দলে দেখতে আসেন এবং মানবিক সহযোগিতা দেন ও অব্যাহত রাখছেন। কিন্তু তারা মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিচারের কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেননি বা করতে পারেননি। এমনকি ‘ওআইসি’ সদস্যভুক্ত ৫৬টি দেশের মধ্যে গাম্বিয়া ছাড়া আর কোনো মুসলিম রাষ্ট্রও কার্যত এগিয়ে আসেনি। গাম্বিয়া আফ্রিকার একটি ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশ। জনসংখ্যা মাত্র ২০ লাখ।
মানচিত্রে অনুল্লেখযোগ্য এই দেশটির বিচারমন্ত্রী আবু বাকার তাম্বাদু গত বছর রোহিঙ্গাদের দেখতে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর ‘আইসিজে’তে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। ফলে গত ১৪ নভেম্বর ‘আইসিসি’ এই অপরাধের পূর্ণ তদন্তের নির্দেশ দেন। পরে গত ডিসেম্বরের ১০ থেকে ১২ তারিখে ‘আইসিজে’তে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এতে উভয়পক্ষের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ আইনজীবীরা অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক আদালতের ১৫ জন স্থায়ী বিচারপতির সাথে মিয়ানমার ও গাম্বিয়ার দু’জন অ্যাডহক বিচারপতি মামলার শুনানি গ্রহণ করেছেন। এই শুনানিতে মিয়ানমারের প্রকৃত সরকারপ্রধান এবং নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অং সান সু চি শুনানিতে অংশ নেন। ২৩ জানুয়ারি ‘আইসিজে’ অন্তর্বর্তীকালীন রায় দিয়েছেন।
এই রায় পৃথিবীর মানবাধিকার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইবে। পূর্ণাঙ্গ বিচারকার্য সম্পন্ন করতে প্রায় পাঁচ-ছয় বছর লেগে যেতে পারে। কাজেই এই অন্তর্বর্তী রায়টি রোহিঙ্গাদের জাতিগত নিধন ও গণহত্যার বিপদ থেকে সুরক্ষার ঢাল হিসেবে কাজ করবে বলে প্রতীয়মান হয়। ১৯৪৮ সালের গণহত্যা কনভেনশনে গাম্বিয়া ও মিয়ানমার উভয়ই স্বাক্ষরকারী দেশ। ‘আইসিজে’ পূর্ণাঙ্গ বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য চার দফা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মিয়ানমারকে আদেশ দেন : ১. গণহত্যা সনদ অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের হত্যাসহ সব ধরনের নিপীড়ন থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে। ২. সেনাবাহিনী বা অন্য কেউ যাতে গণহত্যা সংঘটন ও ষড়যন্ত্র করতে কিংবা উসকানি দিতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। ৩. গণহত্যার অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত সব সাক্ষ্যপ্রমাণ সংরক্ষণ করতে হবে। ৪. চার মাসের মধ্যে এই আদেশ অনুযায়ী মিয়ানমার সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা আদালতকে জানাতে হবে এবং পরে প্রতি ছয় মাস অন্তর একই প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে (দৈনিক প্রথম আলো, ২৪.০১.২০২০)।
সব দিক বিবেচনায় এই অন্তর্বর্তী রায় মানতে মিয়ানমার বাধ্য, যদি তারা সভ্য হয়ে থাকে। এই রায়ের মাধ্যমে বিশ্বমানবতার জয় হয়েছে। আর রোহিঙ্গাদের বিশাল জনগোষ্ঠী মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সনদ পেয়েছে। কিন্তু দুঃখ হলো, বিশ্বে মানবাধিকারের এত বড় বড় প্রবক্তা, ধারক ও বাহক থাকলেও কোনো দেশ এই ভূলুণ্ঠিত মানবতার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি এত দিনেও। ক্ষুদ্র একটি দরিদ্র রাষ্ট্র এই বিচার চেয়ে এগিয়ে এসেছে। এতে ধন্য হয়েছে মূলত মানবতা। আমাদের দেশ মামলার এই রায় থেকে সুবিধা নিতে হবে। কারণ, এখন রোহিঙ্গা সমস্যা আর কোনোভাবেই নিছক দ্বিপক্ষীয় বিষয় নয়। এটি এখন স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সমস্যা। কাজেই মানবিক সহমর্মিতায় আশ্রয় পাওয়া যে তেরো লাখ রোহিঙ্গা বর্তমানে আমাদের দেশে রয়েছে, তাদের নিরাপদ পুনর্বাসনের জন্য আমাদের এখন সরাসরি বিশ্বদরবারের সহযোগিতা নিতে হবে। আর বিশ্ববাসীকে স্বীকার করতে হবে যে, গাম্বিয়া নামক দেশটি পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট্ট হলেও মহাক্ষমতাধর দেশগুলোর কাজের চেয়েও অনেক বড় কাজটি করতে সফল হয়েছে।
লেখক : নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং পিএইচডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়


























